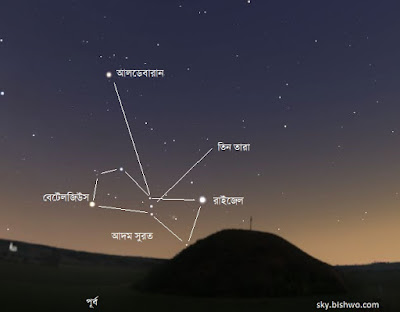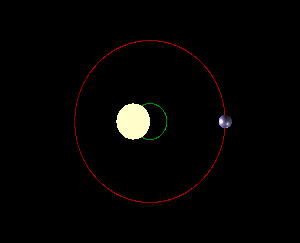|
| ল্যাপটপ চলছে সূর্যের আলোয়। সত্যি বলছি কিন্তু |
প্রশ্নটার উত্তর সোজাসুজি চিন্তা না করে চলুন, খেলার মাঠ থেকে একটা চার বছরের বাচ্চাকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে ধরে নিয়ে আসি। কেন? কারণ, এখন প্রশ্নটার উত্তর দেবার সময় যখনই আমি মনে করব উত্তর যথেষ্ট হয়েছে, তখনই ও আবার প্রশ্ন করবে, 'কেন?'
চার বছরের বাচ্চারা এমনইতো করবে। এর ফলে আমরা প্রশ্নটার সঠিক উত্তর পাবো আশা করি। ওর নাম দিলাম বল্টু। সবাই ওকে হাই বলুন!
অতএব, প্রশ্নটার উত্তরে প্রথমেই বললাম, 'কারণ, আমি ল্যাপটপটা চালু করেছি।'
বল্টুঃ কেন?
আমিঃ ভালো প্রশ্ন করেছো, বল্টু। আমি এটা চালু করেছি যাতে আমি লেখাটা লিখতে পারি। আর আসলে সত্য কথা হল, আমার ল্যাপটপ সব সময় চালুই থাকে। আমি একে কখনো শাট ডাউন দেই না।
বল্টুঃ কেন?
আমিঃ কারণ আধুনিক ল্যাপটপগুলোকে বন্ধ করতে হয় না। আর আমি এমনিতেই বন্ধ করি না, এটা আমার অলসতা আর ল্যাপটপের প্রতি ভালোবাসা।
বল্টুঃ কেন?
আমিঃ আমি আসলে একটু খামখেয়ালী মানুষ, এলোমেলোভাবে চলিতো। কোনো কিছু গোছগাছ করে রাখি না।
বল্টুঃ কেন?
আমিঃ কারণ আমি এখনো বড়োদের মতো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইনি।
বল্টুঃ কেন?
আমিঃ আমার বয়স এখনো খুব বেশি হয়নি, ২৫ ও ক্রস করেনি।
আরে! হচ্ছেটা কী? আমরাতো প্রশ্নটা থেকে সরে যাচ্ছি। এমন তো হবার কথা ছিল না। বল্টু ঠিকভাবে প্রশ্ন করছে না।
দেখো, বল্টু, তোমাকে শুধু 'কেন?' 'কেন?' করার জন্যে নিয়ে আসিনি। তোমাকে সঠিক প্রশ্ন করে ব্যাপারটার গভীরে যেতে হবে।
বল্টুঃ কেন?
আমিঃ কারণ আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতাগুলো পাঠকদের সামনে ফাঁস করার জন্যে তোমাকে আনিনি। আমাদেরকে সঠিক বিষয়টি পাঠকদেরকে জানাতে হবে।
বল্টুঃ কেন?
না, হচ্ছে না। এই বল্টুকে দিয়ে হবে না। বল্টুকে মায়ের কোলে রেখে এসে আমরা বরং ছয় বছরের আরেকটি বল্টু নিয়ে আসি। চার বছরের বাচ্চারা কেমন হয়, ভুলে বসে আছি। আবার শুরু করি।
আমিঃ ল্যাপটপ চালু আছে কারণ এতে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে।
বল্টুঃ বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কেন?
আমিঃ কারণ এটা পাওয়ার কর্ডের সাথে যুক্ত আছে, যেটি আবার ওয়াল সকেটের সাথে যুক্ত।
বল্টুঃ ওয়ালের সকেটে বিদ্যুৎ এল কীভাবে?
আমিঃ কারণ এটা ঢাকা শহরের ইলেকট্রিক গ্রিডের সাথে যুক্ত আছে।
বল্টুঃ ঢাকা শহরের গ্রিডে বিদ্যুৎ এল কোথা থেকে?
হুম! ছয় বছরের বল্টুকে দিয়ে কাজ হচ্ছে। এবার তাহলে আমাদেরকে জেনে আসতে হবে মানুষ কীভাবে ইতিহাসের পরিক্রমায় বিদ্যুৎ শক্তিকে হাত করতে পারল।
এই ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা চলে।
১. অনেক অনেক প্রাচীন যুগে শক্তির ব্যবহার- যখন হাত দিয়ে কষ্ট করে সব কাজ করাব হত।
প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরা আসলেই জানত না যে কীভাবে খুব সহজে কোনো কাজ করে ফেলা যায়।
২। কিছুটা প্রাচীন যুগ- যখন মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে সরাসরি ব্যবহার করা শিখল।
একটা সময় এসে মানুষ বুঝতে পারল, তারা প্রকৃতির কিছু শক্তি কাজে লাগিয়ে নিজেদের কষ্ট অনেক কমিয়ে আনতে পারে। এর অন্যতম আদিম উদাহরণ হল আগুণের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন। এটা ঘটেছিল ১ লাখ ২৫ হাজার বছর থেকে ৪ লাখ বছর আগে (একেকজন অবশ্য একেক উত্তর দেবে এর)।
ইদানিং প্রমাণ পাওয়া গেছে যে ৫ হাজার বছর আগে থেকেই মানুষ বায়ুকল, বাঁধ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাকৃতিক শক্তি থেকে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে স্টিম ইঞ্জিনের মতো অতি আধুনিক (তুলনামূলক) প্রযুক্তির সাহায্যে নৌযান ও লোকোমোটিভ চালনা শুরু হয়।
এগুলো হল প্রাকৃতিক শক্তির সরাসরি ব্যবহার। এদের অসুবিধা ছিল, এদেরকে ব্যবহার করতে হত এর উৎপাদনের স্থান এবং সময়েই। যেমন আগের দিনের বায়ুকল ঘুরত এবং এই ঘূর্ণন বলকে দিয়ে পানি ওঠানো বা শস্য মাড়াইয়ের কাজে লাগানো হত। এমন জিনিসের ব্যবহার কিন্তু আজো ফুরিয়ে যায়নি। একবার ব্ল্যাকআউটের কথাই চিন্তা করুন। আপনার চুলা ও এর উত্তাপ, টয়লেট (যেখানে ফ্ল্যাশ করার জন্যে কাজে লাগে অভিকর্ষ), কাঠের আগুন বা মোমবাতি বা গাড়ি- সবকিছুই প্রকৃতি থেকে সরাসরি শক্তি নিচ্ছে। মাঝখানে আর কিছু নেই।
৩। আধুনিক যুগে শক্তি উৎপাদন- বড়ো মাপে এবং পরোক্ষভাবে।
১০০ আগে বছর মানুষ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে শিখলে বিশ্বে এল যুগান্তকারী পরিবর্তন। ইলেকট্রিক গ্রিডের মাধ্যমে শক্তির সরবরাহ ছড়িয়ে পড়ল দূর দূরান্তে। মানুষের ইতিহাসে হয়ত এটাই সবচেয়ে বড়ো একক মাইলফলক।
শিল্পের প্রয়োজনে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত করা, একে বিদ্যুতে পরিণত করা, দূরে পাঠিয়ে দেওয়া এবং পরে আবার সুবিধা মতো যে কোনো শক্তিতে রূপান্তর করা সহজ হয়ে গেল। দেশের এক প্রান্তের উত্তপ্ত কয়লা আরেক প্রান্তের হিমাগারকে শীতল রাখছে। আধুনিক উইন্ডমিল শুধু পানি তুলতে বা শস্য ভাঙতেই কাজে লাগছে না, এ থেকে বিদ্যুতও পাওয়া যাচ্ছে, যা দিয়ে করা যাচ্ছে প্রায় সব কিছু।
আমার যে ল্যাপটপ চলছে, হতে পারে এর বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া গেছে কয়লা পুড়িয়ে, পরমাণু ভেঙে অথবা বাতাস বা নদীর পানির প্রবাহ থেকে। আমার তাতে কিছু যায় আসে না। এ শক্তিগুলো সবাই আমার কাছে এসে এক হয়ে যায়- আমি যখনই প্লাগ যুক্ত করি, পাই বিদ্যুৎ।
এই দিক থেকে বলা যায় যে, দামের জগতে টাকার যে ভূমিকা, শক্তির জগতে বিদ্যুতের ভূমিকা তাই।
অতএব, এ কারণেই ঢাকাসহ বিশ্বের বড়ো বড়ো প্রায় সব শহরেই ইলেকট্রিক গ্রিড আছে।
বল্টুঃ ইলেকট্রিক গ্রিডে বিদ্যুৎ আছে কেন?
আমিঃ কারণ ওটা পাওয়ার প্ল্যান্টের সাথে যুক্ত আছে, যা গ্রিডে বিদ্যুৎ পাঠাচ্ছে।
বল্টুঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট বিদ্যুৎ বানায় কীভাবে?
হুম, এখন শক্তির সংরক্ষণশীলতার নীতি বলতে হয়। শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, বরং এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন করা যায় মাত্র। এর অর্থ হল, মানুষ শক্তি তৈরি করতে পারে না, তারা শক্তির প্রচলিত রূপকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে পারে। অতএব, বিদ্যুৎ তৈরির একমাত্র উপায় হল শক্তির প্রচলিত কোনো উৎসকে বিদ্যুতে রূপান্তর করা।
সাধারণত যে কয়ভাবে পাওয়ার প্ল্যান্ট কাজ করে তা হলঃ
১. এক ধরনের নবায়নযোগ্য এনার্জি প্ল্যান্ট (জলবিদ্যুৎ (Hydroelectric), বায়ু বা সৌর)। এ থেকে বিদ্যুতের সামান্য অংশই পাওয়া যায়। আমেরিকায় ১১% বিদ্যুৎ পাওয়া যায় এটি থেকে।
২। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট। এ থেকে পুরো বিশ্বের ২.৮ % বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। অবশ্য আমেরিকায় এর ব্যবহার তুলনামূলক অনেক বেশি— ২১%।
৩। বিশ্বের মোট বিদ্যুৎ শক্তির প্রায় ৮০% ই পাওয়া যায় ফসিল ফিউল বা জীবাশ্ম জ্বালানি— কয়লা, গ্যাস, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি থেকে।
এ কারণে,
গাণিতিক সম্ভাবনার কথা বললে আমি বলব যে, আমার ল্যাপটপ চালু আছে হয়ত কোনো জীবাশ জ্বালানির কারণে। আপনার ক্ষেত্রেও একই কথা। আপনি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন, হয়ত ফসিল ফিউল প্ল্যান্টের কল্যাণেই চলছে আপনার ল্যাপটপ।
বল্টুঃ জীবাশ্ম জ্বালানি বা ফসিল ফিউল প্ল্যান্ট কীভাবে বিদ্যুৎ তৈরি করে?
এটা করা হয় জীবাশ্ম জ্বালনি পুড়িয়ে। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে অবশ্য কয়লা বা প্রাকৃতিক গ্যাসই শুধু কাজে লাগানো হয়। তেল দরকার হয় পরিবহনের কাজে। পাওয়ার প্ল্যান্টে কয়লা বা গ্যাস পুড়িয়ে বিপুল পরিমাণ পানিকে উত্তপ্ত করা হয়। এরপর ফুটন্ত বাষ্পকে পাঠানো হয় টারবাইনে (বড় প্রপেলার), যার ফলে এটি ঘুরতে থাকে। টারবাইনটি তামার তার দ্বারা প্যাঁচানো থাকে এবং একে ঘিরে থাকে চুম্বক। টারবাইন ঘোরার সময় তামার কুণ্ডলীও ঘুরতে থাকে। এর ফলে বিদ্যুতের স্রোত তার বেয়ে প্ল্যান্ট থেকে বেরিয়ে আসে। পোঁছে যায় শহরের ইলেকট্রিক গ্রিডে।
অতএব, কয়লার মতো জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত আমার ল্যাপটপ চালু করা হয়েছে।
বল্টুঃ তুমি না বললে, শক্তি তৈরি করা যায় না, শুধু রূপান্তর করা যায়- তাহলে কয়লাকে পুড়িয়ে যে শক্তি পাওয়া গেল তা কোথেকে এল?
বাবুটাতো ভালোই ভোগান্তি দিচ্ছে। ফলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil fuel) আসলে কী?
জীবাশ্ম জ্বালানি হল ত্রিশ থেকে ছত্রিশ কোটি বছর আগের কার্বোনিফেরাস যুগের গাছের ধ্বংসাবশেষ, যে সময় ডাইনোসরদেরও অস্তিত্ব ছিল না। অধিকাংশ গাছই মারা যাবার পরপরই পচে ও ক্ষয় হয়ে গিয়ে এদের ভেতরের শক্তি নির্গত করে দেয়। কার্বোনিফেরাস যুগের অধিকাংশ গাছ, শৈবাল এবং ক্ষুদ্র জীব জলাশয়ে বা সমুদ্রে মারা গিয়েছিল। এরপর এরা তলায় পৌঁছে গিয়ে বালু, কাদা ও অন্যান্য জিনিসের নিচে চাপা পড়ে যায়। এ সময়জুড়ে এরা নিজেদের সাথে বহন করতে থাকে শক্তি। বছরের পর বছর ধরে এই মৃত জিনিসের উপর আরো বেশি বেশি কাদা, বালি, পাথর ইত্যাদি জমতে জমতে তীব্র চাপে এরা গ্যাস, কয়লা ও তেলে পরিণত হয়। যেই শক্তি নিয়ে সেই গাছগুলো মারা গিয়েছিল তা আজো বিদ্যমান রয়েছে— শুধু এর রূপ এখন জীবাশ্ম জ্বালানি রূপে রাসায়নিক শক্তি।
অতএব, সবকিছুর মূলে আছে সেই সময়ের সেই গাছগুলো যা থেকে চলছে বর্তমানের পাওয়ার প্ল্যান্ট।
বল্টুঃ কিন্তু শক্তি বা এনার্জি আসল কোথা থেকে? সেই প্রাচীন গাছগুলোই বা শক্তি পেলো কোথায়?
ঠিক যেভাবে বর্তমানে গাছে শক্তি প্রবেশ করে- সালোকসংশ্লেষণ। ব্যাপারটা খুবই সহজ।
সূর্যের আলো গাছের মধ্যে প্রবেশ করে কার্বন ডাই অক্সাইডকে ভেঙে ফেলে। এর ফলে কার্বন ভেতরে থেকে গিয়ে পদার্থ তৈরি করে এবং অক্সিজেন উপজাত আকারে বেরিয়ে আসে। অণুর এই ভাঙনের সময় গাছ সূর্য থেকে রাসায়নিক শক্তি গ্রহণ করে। এটা গাছের মধ্যেই থেকে যায়। আমরা গাছের গুড়ি পোড়ানোর সময় এই প্রক্রিয়াকেই উল্টো দিকে পরিচালিত করে দেই মাত্র। অক্সিজেন ও কার্বন জায়গা বদল করে। ভেতরের সঞ্চিত সৌরশক্তি আগুনের আকারে বের হয়ে পড়ে। আগুন হল সূর্যের আলো ও উত্তাপ, যা কাঠ থেকে নির্গত হবার আগে বহু দিন যাবত এর মধ্যে সঞ্চিত ছিল।
জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর সময় ঠিক এটিই ঘটে। তবে গাছের বদলে জীবাশ্ম জ্বালানিতে সঞ্চিত সৌরশক্তির বয়স ৩০ কোটি বছর হয়ে গেছে। ফলে এ থেকে প্রাপ্ত শক্তিও ত্রিশ কোটি বছরের পুরনো।
অতএব, আমার ল্যাপটপ চলছে ত্রিশ কোটি বছরের পুরনো সৌরশক্তি দিয়ে।
বল্টুঃ আচ্ছা বুঝলাম, প্রাচীন সূর্য থেকে এই শক্তি এসেছে। কিন্তু সেই শক্তিটা আসল কোথা থেকে?
সূর্যের শক্তি আসলে এর কেন্দ্রে চলমান ফিউশন বিক্রিয়ার ফসল। এ পক্রিয়ায় তীব্র চাপের প্রভাবে পরমাণু জোড়া লেগে একটি একক পরমাণু গঠিত হয়। পরিণামে বিমুক্ত হয় প্রচুর পরিমাণ শক্তি। এটা হল নিউক্লিয়ার ফিসান (ভাঙন) বিক্রিয়ার বিপরীত, যেখানে বড় পরিমাণু ভেঙে যায় (নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট এভাবে কাজ করে)।
জিনিসটা ঘটে এভাবেঃ
 |
| সূর্য যেভাবে কাজ করে |
অতএব, নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ায় সৃষ্ট শক্তির ফলে সূর্যের কেন্দ্রমণ্ডল থেকে ফোটন (আলোক কণা) বেরিয়ে আসে। এই ফোটন সূর্যের পৃষ্ঠে পৌঁছতে এক লক্ষ বছর লাগিয়ে দেয়, কিন্তু তারপর পৃথিবীতে আসতে আর মাত্র আট মিনিট লাগে। এর পরেই গাছ সেটা পায়।
বল্টুঃ আচ্ছা, সেই শক্তি- মানে নিউক্লিয়ার ফিউশন— ওটা এল কোথা থেকে?
সূর্যের কেন্দ্রে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া শুরু হবার কারণ হচ্ছে এর তীব্র মহাকর্ষ চাপ।
বল্টুঃ মহাকর্ষটা আবার কী?
বল্টু, তুমি এখনো অনেক ছোট।
মহাকর্ষ হল বক্র স্থান- কাল। এ বক্রতা তৈরি হয় বস্তুর উপস্থিতিতে। আর সূর্যের মতো বিশাল বস্তুর ক্ষেত্রে এই বক্রতার পরিমাণও বিশাল।
অতএব, ল্যাপটপের পাওয়ার সরবরাহের পেছনে একটি সত্যিকারের উৎস আছে। এটা হল সূর্যের দ্বারা সৃষ্ট স্থান- কালের তীব্র বক্রতা। এর কারণে শুরু হয় নিউক্লিয়ার ফিউশন এবং তার এক লক্ষ বছর পরে গাছ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে সেই শক্তি গ্রহণ করে। সেই শক্তি এরপর মৃত গাছের মধ্যে অবস্থান করে ধীরে ধীরে কয়লার মতো জীবাশ্মে পরিণত হয়। এই কয়লা ৩০ কোটি বছর পরে কোল মাইনাররা বের করে আনে, বয়ে নিয়ে আসা হয় পাওয়ার প্ল্যান্টে।
একে পুড়িয়ে প্রাচীন সূর্যের মতোই আলো ও উত্তাপ পাওয়া যায়। এই উত্তাপ কাজে লাগিয়ে পানিকে গরম করা হয়, যা তখন স্টিম বা বাষ্পে পরিণত হয়। এটি জেনারেটরের ভেতরে থাকা টারবাইনকে ঘোরায়। এর ফলে শক্তি বের হয়ে বিদ্যুৎ আকারে চলে আসে ইলেকট্রিক গ্রিডে। এটাই পরে লাইন বেয়ে চলে আসে আমার বাসার ওয়ালে। পাওয়ার কর্ড ল্যাপটপে লাগানোর সাথে সাথে এটি চালু হবার শক্তি পায়।
তবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সূর্যের প্রাচীন মহাকর্ষের এই প্রভাব নন-ইলেকট্রিক এনার্জির ক্ষেত্রেও বলা চলে। গাড়ির হুডের নিচেও অবস্থান করছে একটি মিনি পাওয়ার প্ল্যান্ট। এটি তেল থেকে আসা গ্যাসোলিন পুড়িয়ে প্রাচীন সেই শক্তিতে ফিরিয়ে আনছে। এমনকি একটি মোমবাতি বা শক্তির যে কোনো রূপের ক্ষেত্রেই এটি ঘটছে।
একই ঘটনা চলছে আমাদের দেহেও। আমি এটি লিখতে পারছি কেন? কারণ আমার বডিতে আমার খাওয়া খাবারের শক্তি আছে। এই শক্তি আগে ছিল উদ্ভিদ বা প্রাণীতে, যার ফলে আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি সেই সালোকসংশ্লেষণে। তবে এই ক্ষেত্রে সালোকসংশ্লেষণ নতুন। এর অর্থ হল, আমার আঙ্গুলের পাওয়া সূর্যের আলো খুব নতুন, সূর্যের কেন্দ্র থেকে আসতে সময়টুকুর কথা বাদ দিলে। যে মহাকর্ষের ফলে সেই ফিউশন শুরু হয়েছিল, তা কিন্তু এক লক্ষ বছরেরই পুরনো।
তো, বল্টু, বুঝলেতো?
বল্টুঃ বুঝলাম। কিন্তু দাঁড়াও, বস্তুর কারণে স্থান- কাল বেঁকে যায় কেন?
সেরেছে! এই ছোকরার হাত থেকে কীভাবে বাঁচি! ঐ চার বছরের বাচ্চাইতো ভালো ছিল।
সূত্রঃ